স্কটল্যান্ডের গ্লাসগোতে গত বছর অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন-বিষয়ক সম্মেলন কপ২৬-এ ক্লাইডব্যাংক ডিক্লারেশনে স্বাক্ষর করে ২২টি দেশ। এর মধ্যে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জার্মানি, জাপানের মতো শিল্পোন্নত দেশগুলো। এই ঘোষণার মূল লক্ষ্য সমুদ্র পরিবহন খাতে কয়েকটি গ্রিন করিডোর প্রতিষ্ঠা।
গ্রিন করিডোর কোনো বৈশ্বিক সমাধান নয়। তবে একটি-দুটি করে যখন বিশ্বের সব ট্রেডিং রুটই যখন গ্রিন করিডোর হয়ে যাবে, তখন সেটি নিঃসরণ কমানোর বৈশ্বিক উদ্যোগেরই অংশ হয়ে যাবে।
কেবল যে ক্লাইডব্যাংক ডিক্লারেশনে স্বাক্ষরকারী দেশগুলোই গ্রিন করিডোরকে গুরুত্ব দিচ্ছে অথবা কেবল তারাই যে এর সুবিধাভোগী হবে, তা নয়। এই ঘোষণায় স্বাক্ষর না করলেও যুগোপযোগী ধারণাটির সঙ্গে একাত্মতা পোষণ করে গ্রিন করিডোর প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী অবস্থানে রয়েছে চীন। পরিকল্পনাধীন রয়েছে আরও কিছু করিডোর। আর এই ধরনের উদ্যোগের সংখ্যা বেশি হলে তার ফলাফল যে বিশ্বজনীন হবে, তা বলাই বাহুল্য।
নিঃসরণে বৈশ্বিক উদ্বেগ
বৈশ্বিক উষ্ণায়ন এখন বিশ্বনেতাদের মাথাব্যথার বড় কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর এই উষ্ণায়নের অন্যতম কারণ গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ। বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে আবহাওয়া ও জলবায়ুতে অস্বাভাবিক পরিবর্তন আসছে। উষ্ণায়নের ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়ছে এবং বিশ্বকে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক সুর্যোগের মোকাবিলা করতে হচ্ছে।
গ্রিনহাউস গ্যাসের পরিমাণ যত বাড়বে, বায়ুম-ল তত বেশি উষ্ণ হয়ে উঠবে। গ্রিনহাউস অ্যাফেক্টের কারণে সূর্য থেকে আসা তাপশক্তি ভূপৃষ্ঠকে উত্তপ্ত করে তোলে এবং ভূপৃষ্ঠ থেকে বিকরিত তাপশক্তির বেশির ভাগই পুনরায় বায়ুম-লে ফিরে আসে।
অতিমাত্রায় জীবাশ্ম জ্বালানি দহন, নির্বিচারে বনাঞ্চল ধ্বংস, অপরিকল্পিত শিল্পায়নসহ বিভিন্ন কারণে কার্বন ডাই-অক্সাইড, মিথেন ও নাইট্রাস অক্সাইডের মতো গ্রিনহাউস গ্যাসের পরিমাণ আশঙ্কাজনক হারে বেড়ে গেছে। ফলে বায়ুম-লের তাপমাত্রাও বাড়ছে নিয়ন্ত্রণহীন গতিতে। ১৮৫০ থেকে ১৯৬০ সালের মধ্যে পৃথিবীর বায়ুম-লের তাপমাত্রা বেড়েছে প্রায় পাঁচ গুণ।
বাংলাদেশের ওপর উষ্ণায়নের প্রভাব
পরিবেশবিজ্ঞানীদের মতে, বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দেশের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশে যেসব বড় ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা গেছে, তা মূলত জলবায়ু পরিবর্তনের কারণেই হয়েছে। বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধিই এ পরিবর্তিত জলবায়ুর জন্য দায়ী।
বৈশ্বিক উষ্ণায়ন প্রতিরোধ করা না গেলে
বাংলাদেশকে যেসব ভয়াবহ পরিণতি ভোগ করতে হবে, সেগুলোর মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করার যায় সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির কথা। বায়ুম-লে তাপমাত্রা বেড়ে গেলে সমুদ্রের পানির উষ্ণতাও বেড়ে যাবে। সামুদ্রিত উষ্ণায়নের ফলে হিমবাহসহ বিভিন্ন পর্বতের বরফ গলে যাবে, যার ফলে সমুদ্রস্তরের উচ্চতা বৃদ্ধি পাবে। এর সঙ্গে উপকূলীয় এলাকায় বন্যার প্রকোপ তীব্র হবে।
বাংলাদেশ বিশ্বের বৃহত্তম বদ্বীপ। অসংখ্য নদী এই ভূখণ্ডের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে মিশেছে। গবেষণা বলছে, ভূম-লের তাপমাত্রা ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি পেলে বাংলাদেশের ১৯ শতাংশ ভূমি সমুদ্রগর্ভে বিলীন হয়ে যাবে। বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় ভূপৃষ্ঠের উচ্চততা বৃদ্ধির হার বছরে ৫-৬ মিলিমিটার, যেখানে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে বছরে ৭ মিলিমিটার হারে। ইন্টারগভর্নমেন্টাল প্যানেল অব ক্লাইমেট চেঞ্জের (আইপিসিসি) এক সমীক্ষায় বলা হয়েছে, বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা প্রতি দশকে ৩ দশমিক ৫ মিলিমিটার থেকে ১৫ মিলিমিটার পর্যন্ত বাড়তে পারে। ২১০০ সাল নাগাদ তা ৩০-১০০ সেন্টিমিটারে উন্নীত হতে পারে। তাই বৈশ্বিক উষ্ণায়নের প্রভাবে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি অব্যাহত থাকলে তা যে বাংলাদেশের জন্য ভয়াবহ বিপর্যয় সৃষ্টি করবে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।
জলবায়ু পরিবর্তনের আরেকটি প্রভাব হবে পানির লবণাক্ততা বৃদ্ধি। এছাড়া খরাপ্রবণতার কারণে দেশের উত্তর, উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের নদ-নদীগুলোর পানির প্রবাহ কমে যাবে এবং এসব অঞ্চলে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর অনেক নিচে নেমে যাবে। কৃষিপ্রধান বাংলাদেশের জন্য এ দুটি পরিবর্তনই উদ্বেগজনক। লবণাক্ততা বেড়ে গেলে উপকূলীয় কৃষি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আর মরুভূমির প্রবণতা তৈরি হলে উজানের জমিগুলো পানির অভাবে চাষযোগ্যতা হারাবে।
বাংলাদেশের উপকূলী জনগোষ্ঠীকে প্রতি বছর যে বিষয়টির কারণে আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাতে হয়, তা হলো সামুদ্রিক ঝড় ও জলোচ্ছ্বাস। সাধারণত সামুদ্রিক ঝড় সৃষ্টি হয় উত্তপ্ত বায়ু ও ঘূর্ণিঝড় থেকে। ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টির পেছনে আরও কয়েকটি প্রভাবক কাজ করলেও উষ্ণতা বৃদ্ধিই এর মূল কারণ। বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে সমুদ্রের পানির তাপমাত্রাও ক্রমবর্ধমান হবে। স্বাভাবিকভাবেই সামুদ্রিক ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের তীব্রতাও বেড়ে যাবে।
বৈশ্বিক উষ্ণায়নের জন্য দায়ী সমুদ্রশিল্পও
কেবল যে অপরিকল্পিত নগরায়ন, শিল্প-কারখানার ধোঁয়া, কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র, বনাঞ্চল উজাড় হওয়া ইত্যাদিই উষ্ণায়নের জন্য দায়ী, তা নয়। সমুদ্র পরিবহন খাতকেও এর দায় নিতে হবে। গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণে এই খাতের সংশ্লিষ্টতাও উপেক্ষা করা যাবে না। যদিও বৈশ্বিক নিঃসরণের সামান্য অংশই আসে সমুদ্রশিল্প থেকে। ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম অর্গানাইজেশনের (আইএমও) হিসাব অনুযায়ী, জাহাজ চলাচলের কারণে প্রতি বছর ১০০ কোটি টন গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসৃত হয়, যা বৈশ্বিক নিঃসরণের প্রায় ৩ শতাংশ। তবে এখনই কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা না হলে ২০৫০ সাল নাগাদ নিঃসরণের পরিমাণ ২০০৮ সালের চেয়ে ৩০ শতাংশ বেড়ে যাবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।
বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি প্রতিরোধে জলবায়ু সম্পর্কিত প্যারিস চুক্তি একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ। তাপমাত্রা বৃদ্ধি যেন প্রাক-শিল্পায়ন যুগের চেয়ে ১ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি হতে না পারে, সেই বিষয়ের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে চুক্তিতে। তবে পরিবেশ আন্দোলনকর্মীরা বলছেন, আইএমও নিঃসরণ কমানোর যে লক্ষ্যমাত্রা বেঁধে দিয়েছে, তা প্যারিস চুক্তির উদ্দেশ্য পূরণের জন্য যথেষ্ট হবে না। আইএমওর বর্তমান লক্ষ্যমাত্রায় ২০৫০ সাল নাগাদ নিঃসরণের মাত্রা ২০০৮ সালের তুলনায় মাত্র ৫০ শতাংশ কমানোর কথা বলা হয়েছে। কিন্তু বিশেষজ্ঞরা বলছেন, প্যারিস চুক্তির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য চলতি শতাব্দীর মাঝামাঝি নাগাদ বৈশ্বিক শিপিং খাতকে পুরোপুরি নিঃসরণমুক্ত হতে হবে।
গ্রিন করিডোর যখন আপাত সমাধান
নিঃসরণ প্রতিরোধে আইএমও এখন পর্যন্ত যেসব পদক্ষেপ নিয়েছে, তা পরিবেশ আন্দোলনকর্মীদের খুব একটা খুশি করতে পারেনি। বিভিন্ন প্রভাবকের কারণে আইএমওর সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াটি ধীরগতির। এ কারণে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ এখন নিজেরাই পরিবেশবান্ধব শিপিং খাত গড়ে তুলতে বিভিন্ন উদ্যোগ নিচ্ছে। গ্রিন করিডোর প্রতিষ্ঠা এই উদ্যোগেরই অংশ।
গ্রিন করিডোর নামের মধ্যেই পরিবেশবান্ধবতার আভাস রয়েছে। এটি হলো এমন শিপিং রুট, যেখানে কোনো নিঃসরণ থাকবে না। এসব রুটে চলাচলকারী জাহাজগুলো ব্যবহার করবে সবুজ জ্বালানি। গ্রিন করিডোর আন্তর্জাতিকভাবে বাধ্যতামূলক কোনো পদক্ষেপ হবে না। দুই বা ততোধিক বন্দরের মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে এসব করিডোর গড়ে উঠবে।
২০২৫ সাল নাগাদ অন্তত ছয়টি গ্রিন করিডোর প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে ক্লাইডব্যাংক ডিক্লারেশনে। ২০৩০ সাল নাগাদ আরও কয়েকটি নিঃসরণমুক্ত রুট কার্যকর হবে বলে কপ২৬ সম্মেলনে আশা প্রকাশ করা হয়।
গ্রিন করিডোর কীভাবে উষ্ণায়ন প্রতিরোধে ভূমিকা রাখবে? আগেই বলা হয়েছে, এই করিডোর দিয়ে শীর্ষ শিপিং হাবগুলোর মধ্যে চলাচলকারী জাহাজে কেবল পরিবেশবান্ধব জ্বালানিই ব্যবহার করা হবে। আর এই রূপান্তরের জন্য আইনগত, অবকাঠামোগত ও প্রযুক্তিগত যা কিছু পরিবর্তন আনা দরকার, সংশ্লিষ্ট দেশগুলো তার উদ্যোগ নেবে।
বৈশ্বিকভাবে শিপিং খাতের বিভিন্ন নীতিনির্ধারণের দায়িত্ব যাদের কাঁধে, তাদের জন্য ভবিষ্যৎ করণীয় বিষয়ে গ্রিন করিডোর একটি ভালো উদাহরণ তৈরি করবে। এসব করিডোর সংশ্লিষ্ট দেশগুলোকে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করবে যে, কোন পদক্ষেপ নিলে তা কার্বন নিঃসরণ কমানোর প্রচেষ্টায় ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে। আর এসব পদক্ষেপ কার্যকর হলে আইএমওর মতো নীতিনির্ধারক সংস্থাগুলোও ধারণা পাবে যে, কী ধরনের পরিবর্তন আনলে তা বাস্তবসম্মত হবে।

গ্রিন করিডোরের জন্য কিছু চ্যালেঞ্জ
সবুজ রূপান্তরের ক্ষেত্রে বর্তমানে শিপিং খাতের সামনে সবচেয়ে বড় যে চ্যালেঞ্জ রয়েছে, সেটি হলো পরিবেশবান্ধব জ্বালানিগুলো এখনো জীবাশ্ম জ্বালানির তুলনায় ব্যয়বহুল। যুক্তিসংগতভাবেই জাহাজের মালিক বা অপারেটররা এই বাড়তি ব্যয় বহন করতে আগ্রহী হবে না। অর্থাৎ গ্রহণযোগ্যতার প্রতিযোগিতায় প্রথমেই পিছিয়ে পড়বে সবুজ জ্বালানি।
প্রতিযোগিতা সক্ষমতার এই ফারাক দূর করতে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে কার্বন শুল্ক। ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডনের (ইউসিএল) এনার্জি ইনস্টিটিউট ও ইউনিভার্সিটি মেরিটাইম অ্যাডভাইজরি সার্ভিসেসের (ইউএমএএস) একটি যৌথ গবেষণায় বলা হয়েছে, প্রতি টন কার্বন ডাই-অক্সাইড নিঃসরণের বিপরীতে গড়ে প্রায় ২০০ ডলার শুল্ক আরোপ করা হলে জীবাশ্ম জ্বালানি ও বিকল্প জ্বালানিতে ব্যয়ের এই অসামঞ্জস্যতা অনেকটাই লাঘব হবে।
বর্তমানে বিকল্প জ্বালানিতে রূপান্তর কিংবা নিঃসরণমুক্ত জাহাজ তৈরির ক্ষেত্রে কোনো ধরনের প্রণোদনা চালু নেই। ক্লাইডব্যাংক ডিক্লারেশনের মতো উদ্যোগ সেই ধরনের প্রণোদনার ক্ষেত্র তৈরি করবে। হয়তো তা সমুদ্র পরিবহন খাতকে নিঃসরণমুক্ত করার জন্য যথেষ্ট নয়। তবে নীতিনির্ধারণের পথকে মসৃণ করতে অবশ্যই এই ধরনের উদ্যোগ সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।
গ্রিন করিডোরে দুটি জালানিকে পরিবেশবান্ধব বিবেচনায় এগিয়ে রাখা হচ্ছে। এগুলো হলো-মিথানল ও গ্রিন অ্যামোনিয়া। নবায়নযোগ্য উৎস থেকে উৎপাদন হলে উভয় জ্বালানিই কার্বন নিঃসরণমুক্ত থাকে। অ্যামোনিয়া হলো নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেনের একটি যৌগ, যেটিতে কোনো কার্বন থাকে না। ফলে ইন্টারনাল কম্বাশন ইঞ্জিনে ব্যবহার করা হলে এটি কোনো কার্বন ডাই-অক্সাইড নিঃসরণ করে না। এদিকে মিথানলের সুবিধা হলো, এই জ্বালানিতে চালিত নতুন জাহাজ নির্মাণ অথবা জাহাজের বিদ্যমান জ্বালানি ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করে মিথানলভিত্তিক করে গড়ে তুলতে খরচ হয় তুলনামূলক কম।
শিপিং খাতে সর্বত্র পরিবেশবান্ধব জ্বালানির ব্যবহার বাধ্যতামূলক করার ক্ষেত্রে আরেকটি বড় চ্যালেঞ্জ হলো, অবকাঠামোগত অপ্রতুলতা। এসব জ্বালানির উৎপাদন ও মজুদের জন্য নতুন অবকাঠামো নির্মাণ করতে হবে। এছাড়া জাহাজগুলো যেন বন্দরে রিফুয়েলিং সুবিধা পায়, সে বিষয়টিও নিশ্চিত করতে হবে। বর্তমানে পরিবেশবান্ধব জ্বালানির উৎপাদন খুব কম। এখন বছরে ২০ লাখ টনের কম নবায়নযোগ্য মিথানল উৎপাদন হয়।
মিথানল ও অ্যামোনিয়া দুটোরই অন্যতম উপাদান হাইড্রোজেন। সুতরাং গ্রিন করিডোরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দেশগুলোকে ইলেক্ট্রোলাইজার, ব্যাটারি, নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধি, হাইড্রোজেন স্টোরেজ ইত্যাদি খাতে বিনিয়োগ করতে হবে। আর যেহেতু হাইড্রোজেন এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পরিবহন করা খরচসাপেক্ষ, সেহেতু সংশ্লিষ্ট অবকাঠামো সুবিধাদি স্থাপন করতে হবে করিডোরের সঙ্গে যুক্ত বন্দরে অথবা বন্দরের নিকটবর্তী এলাকায়।
ক্লাইডব্যাংক ডিক্লারেশনে না থাকলেও প্রথম করিডোরে যুক্ত চীন
বিশ্বের সর্ববৃহৎ জাহাজ নির্মাতা দেশ চীন। বিশ্বে সমুদ্রগামী পণ্যবাহী জাহাজের সবচেয়ে বড় বহরটিও তাদের। কিন্তু তারা গ্লাসগো কপ২৬ সম্মেলনে গৃহীত ক্লাইডব্যাংক ডিক্লারেশনে স্বাক্ষর করেনি। বিষয়টি হতাশাজনক হলেও আশাব্যঞ্জক একটি খবরও রয়েছে। আর তা হলো বিশ্বের প্রথম গ্রিন করিডোরের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে চীন।
গ্রিন করিডোরের পক্ষে থেকেও চীন কেন ক্লাইডব্যাংক ডিক্লারেশনে স্বাক্ষর করল না? এ বিষয়ে একটি সম্ভাব্য যুক্তি তুলে ধরেছেন ইন্টারন্যাশনাল কাউন্সিল অন ক্লিন ট্রান্সপোর্টেশনের (আইসিসিটি) মেরিন প্রোগ্রাম টিমের জ্যেষ্ঠ গবেষক শাওলি মাও। তিনি বলেন, চীন মনে করে, সমুদ্রশিল্পে নিঃসরণ কমাতে পরিকল্পনা গ্রহণের বিষয়টি ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম অর্গানাইজেশনের (আইএমও) নিয়ন্ত্রণাধীন থাকা উচিত; কপ২৬ সম্মেলনের আহ্বায়ক ইউএন ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন ক্লাইমেট চেঞ্জের নিয়ন্ত্রণে নয়।
২০২২ সালের শেষ নাগাদ একটি নিঃসরণমুক্ত শিপিং রুট প্রতিষ্ঠার বিষয়ে গত জানুয়ারিতে ঐকমত্যে পৌঁছায় বিশ্বের ব্যস্ততম সমুদ্রবন্দর সাংহাই এবং আমেরিকা’স পোর্ট হিসেবে খ্যাত লস অ্যাঞ্জেলেস বন্দর। সবকিছু পরিকল্পনা অনুযায়ী এগুলে ট্রান্স-প্যাসিফিক করিডোর নামে পরিচিত ব্যস্ততম এই কার্গো রুটটি বিশ্বের প্রথম গ্রিন করিডোর হতে যাচ্ছে।
ট্রান্স-প্যাসিফিক করিডোরে কার্গো পরিবহন হয় লাইনার ট্রেডিং ব্যবস্থায়। লাইনার ট্রেডিং এমন একটি ব্যবস্থা, যেখানে একটি নির্দিষ্ট রুটে নিয়মিত শিডিউল ভিত্তিতে পণ্য পরিবহন করা হয়। এই রুটটি নিঃসরণমুক্ত হলে তা বৈশ্বিক সমুদ্র পরিবহন খাতের জন্য ইতিবাচক পরিবর্তন বয়ে আনবে। কারণ সমুদ্রপথে বৈশি^ক পণ্য পরিবহনের বড় একটি অংশ সম্পন্ন হয় এই রুটে। ২০২০ সালে এই করিডোর দিয়ে মোট ৩ কোটি ১২ লাখ টিইইউ কনটেইনার পরিবহন হয়েছে, যা বিশ্বের মোট কনটেইনার পরিবহনের প্রায় ২১ শতাংশ।
শুধু সাংহাই-লস অ্যাঞ্জেলেসই নয়, বরং চীন গ্রিন করিডোরের মাধ্যমে যুক্ত হতে পারে গুরুত্বপূর্ণ আরও একটি রুটে। সেটি হলো শেনঝেন-লং বিচ রুট। ট্রান্স-প্যাসিফিক করিডোরের চেয়ে এটি আরও দীর্ঘ রুট এটি। এই গ্রিন করিডোরটি প্রতিষ্ঠার বিষয়ে এরই মধ্যে কৌশলগত সম্ভাব্যতা যাচাই সম্পন্ন হয়েছে। এই সমীক্ষায় রুটটিতে ২০১৫ সালের শিপ ট্রাফিক পর্যালোচনা করা হয়েছে। এতে দেখা গেছে, ৯৯ শতাংশ যাত্রার ক্ষেত্রে জাহাজগুলোর জ্বালানিধারণ সক্ষমতা ও পরিচালন কার্যক্রমে সামান্য কিছু পরিবর্তন আনলেই সেগুলো হাইড্রোজেন জ্বালানি দিয়ে পরিচালনা সম্ভব।
বিশেষজ্ঞরা বলছেন, দীর্ঘ রুটে গ্রিন করিডোর স্থাপনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় যে চ্যালেঞ্জ রয়েছে, সেটি হলো জাহাজগুলোর রিফুয়েলিং সুবিধা নিশ্চিতকরণ। কারণ প্রথাগত জ্বালানি একবার ভর্তি করে যতটা পথ পাড়ি দেওয়া যায়, বিকল্প জ্বালানি গুলো দিয়ে সেটি সম্ভব নয়। ফলে গ্রিন করিডোরের সঙ্গে যুক্ত বন্দরগুলোকে অবশ্যই সুবিধাজনক রিফুয়েলিং পয়েন্ট স্থাপন করতে হবে। যেমন শেনঝেন-লং বিচ রুটের মাঝামাঝি স্থান আলাস্কা উপকূলের অ্যালিউশিয়ান আইল্যান্ড জাহাজগুলোর রিফুয়েলিং পয়েন্ট হিসেবে আদর্শ জায়গা হতে পারে।

পরিকল্পনায় রয়েছে আরও করিডোর
গ্রিন করিডোর ধারণাটি এখনো নতুন। তবে এরই মধ্যে সম্ভাবনাময় আরও কয়েকটি করিডোর স্থাপনের কার্যক্রম চলমান। এর মধ্যে অস্ট্রেলিয়া-জাপান আয়রন ওর করিডোর ও এশিয়া-ইউরোপ কনটেইনার করিডোর অন্যতম।
অস্ট্রেলিয়া-জাপান সমুদ্রপথটি বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ ড্রাই বাল্ক ট্রেড রুট। এই পথে প্রতি বছর দুই দেশের মধ্যে প্রায় সাড়ে ছয় কোটি টন আকরিক লোহা পরিবহন হয়। অস্ট্রেলিয়া এরই মধ্যে হাইড্রোজেন জ্বালানি খাতে মোটা অংকের বিনিয়োগ শুরু করেছে। তারা ২০৩০ সাল নাগাদ ২৯ গিগাওয়াট ইলেক্ট্রোলাইজার ক্যাপাসিটি স্থাপনের পরিকল্পনার ঘোষণা দিয়েছে। এই ক্যাপাসিটির বেশির ভাগই থাকবে দেশটির গুরুত্বপূর্ণ বন্দরগুলোর নিকটবর্তী অবস্থানে।
এশিয়া-ইউরোপ করিডোর বিশ্বের দীর্ঘতম শিপিং রুটগুলোর একটি। বর্তমানে অন্য যেকোনো রুটের চেয়ে এই করিডোরে নিঃসরণ বেশি হয়। এই পথে সম্ভাবনাময় বেশ কয়েকটি রিফুয়েলিং পয়েন্ট রয়েছে, যা একে গ্রিন করিডোর হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে সহায়তা করবে। ২০৩০ সাল নাগাদ এই করিডোরে ৬০ গিগাওয়াটের বেশি হাইড্রোজেন ইলেক্ট্রোলাইজার ক্যাপাসিটি প্রতিষ্ঠার ঘোষণা এরই মধ্যে দেওয়া হয়েছে।
এদিকে আগামী দশকের মধ্যেই আন্তঃইউরোপীয় কয়েকটি গ্রিন করিডোর চালু হবে বলে বিশ্লেষকরা আশা করছেন। ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) এরই মধ্যে শিপিং খাতকে নিঃসরণমুক্ত করার জন্য বেশকিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এসব উদ্যোগের মধ্যে রয়েছে ইইউ অঞ্চলে টেকসই জ্বালানির ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা এবং জোটটির এমিশন ট্রেডিং স্কিমে (ইটিএস) সামুদ্রিক নিঃসরণকে অন্তর্ভুক্ত করা।
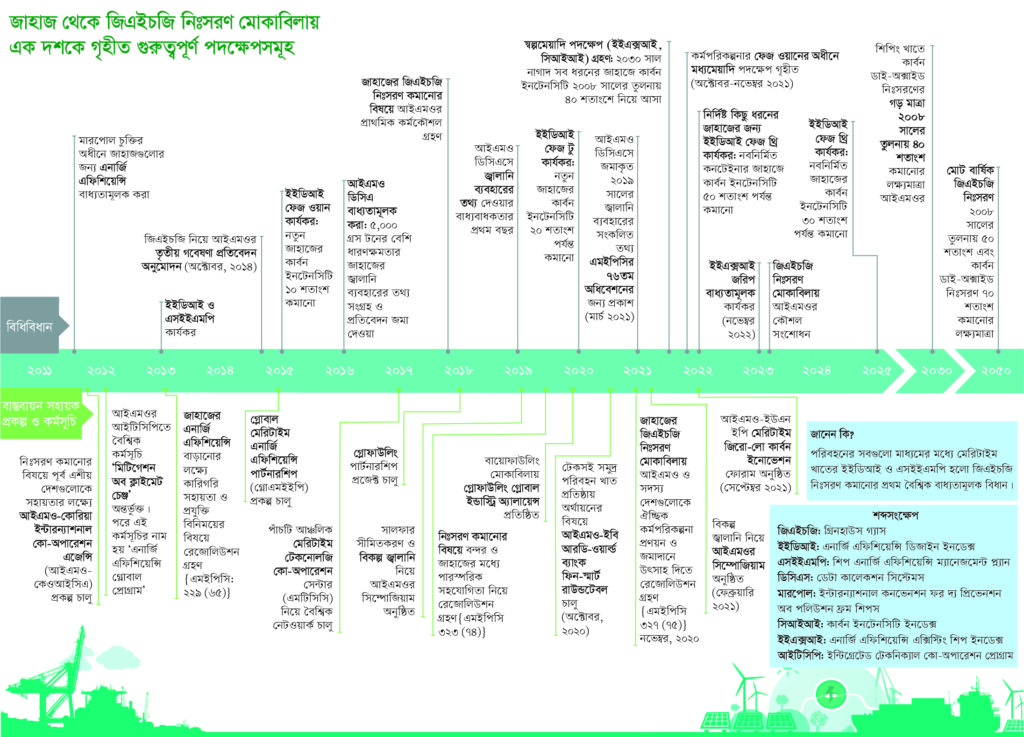
আইএমও প্রসঙ্গ
দেশগুলো নিজস্ব উদ্যোগে নিঃসরণ কমানোর পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে। এ অবস্থায় আইএমও কি কেবল পার্শ্বচরিত্র হয়েই থাকবে? বিশেষজ্ঞরা বলছেন, গ্রিন করিডোরগুলো আইএমওর কাজে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করবে না। বরং গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ কমানোর লক্ষ্যে বৈশ্বিক শিপিং খাতকে নিয়ন্ত্রণ এবং দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণের ক্ষেত্রে এসব করিডোর আইএমওর জন্য সহায়ক উদ্যোগ হিসেবে কাজ করবে।
জাতিসংঘের সমুদ্রবিষয়ক সংস্থা আইএমও যেকোনো উদ্যোগ নিলে তা বাস্তবায়নের আগে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর ঐকমত্যের প্রয়োজন হয়। এ কারণে সংস্থাটির কার্যক্রমের গতি একটু ধীর। বিশেষজ্ঞরা আশা করছেন, গ্রিন করিডোরগুলো আইএমওর সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াটি ত্বরান্বিত করবে। তারা বলছেন, যত বেশি গ্রিন করিডোর হবে, আইএমওর কর্মতৎপরতা তত বাড়বে। একই সঙ্গে কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সরকারগুলোও তত বেশি পরিবেশবান্ধব পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হবে। আসলে গ্রিন করিডোর ও আইএমও পৃথক কোনো সত্তা নয়, বরং একই বাস্তুতন্ত্রের অংশ।
উপসংহার
উষ্ণায়ন কোনো একটি দেশের বা অঞ্চলের সমস্যা নয়। এটি বৈশ্বিক সমস্যা। এ কারণে উষ্ণায়ন প্রতিরোধে কেবল একটি-দুটি দেশ উদ্যোগ নিলে চলবে না। জলবায়ু সুরক্ষার উদ্যোগগুলো হতে হবে সমন্বিত।
তবে বিভিন্ন কারণে বৈশ্বিক পেক্ষাপটে নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নে বিলম্ব হয়। আইএমওকেও এই ধরনের জটিলতার মধ্য দিয়েই যেতে হয়। তাই নিঃসরণ কমানোর পদক্ষেপের জন্য কেবল বৈশ্বিক সংস্থাটির অপেক্ষায় বসে থাকলে চলবে না। বরং তারা পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতেও কিছু উদ্যোগ নিতে পারে। গ্রিন করিডোর এই বাস্তবতারই উদাহরণ হতে যাচ্ছে।
পরিবেশবান্ধব জ্বালানির ব্যবহার নিশ্চিতের মাধ্যমে গ্রিন করিডোরগুলো নিঃসরণ কমাতে অনবদ্য ভূমিকা রাখবে। ভবিষ্যতে এই ধরনের করিডোরের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পেলে তখন শিপিং খাতকে নিঃসরণমুক্ত করা খুব একটা কঠিন হবে না।




